ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর ‘নিন্দিত নন্দন’ - আত্মজীবনী ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের ইতিহাসের গল্প : মোঃ ইয়াকুব আলী
প্রকাশিত:
২৪ নভেম্বর ২০২২ ০৪:২২
আপডেট:
৩ মে ২০২৪ ১২:৫৫

কখনওই ভাবিনি বুক রিভিউ লিখবো। কিভাবে লিখতে হয় তাও জানা ছিল না আমার। কিন্তু ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর নিন্দিত নন্দন পড়ার পর থেকেই মনের মধ্যে একটা তাগাদা অনুভব করছিলাম। এমন বই আমার মনেহয় প্রত্যেকটা বাংলাদেশির জন্য পাঠ বাধ্যতামূলক করে দেয়া উচিৎ। বাংলাদেশে থাকতে এই বইটা প্রকাশের খবর শুনেছিলাম কিন্তু পড়ার সৌভাগ্য হয় নাই। তাই যখন প্রতিবেশী নাজমুল ভাই এবং সন্ধ্যা ভাবির বাড়িতে বইটা পেলাম, পড়ার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলাম না। বইটা ধার নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করছিল।
ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর উপর দিয়ে ১৯৭১ সালের নয় মাসে যে ঝড় বয়ে গেছে সেটা গ্রহন করার মত আমি মানসিকভাবে তৈরি কি না। বইটা ব্যাগে নিয়ে সকাল বিকাল কাজে আসা যাওয়ার পথে সাবধানে পড়ি কারণ একাত্তরের ঘটনার বর্ণনা শুরু হলেই যেন আমি থামতে পারি। এভাবে বইটার প্রথম এক শত পৃষ্ঠা দ্রুতই পড়ে ফেললাম। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে ১৯৭১ সালের ঘটনার বর্ণনা। তাই স্বভাবতই আমাকে থামতে হল। এরপর আমি বইটা মাসের পর মাস ব্যাগে নিয়ে ঘুরলাম কিন্তু আর সাহস করে উঠতে পারলাম না। বেশ কয়েকমাস বইটা ব্যাগে নিয়ে ঘুরার পর দেখলাম বইটার ক্ষতি হচ্ছে, প্রচ্ছদের লেখা মুছে যেতে শুরু করেছে। তাই বইটা আবার নাজমুল ভাইদেরকে ফেরতও দিয়ে দিলাম।
হঠাৎ একদিন খবর পেলাম উনি মারা গেছেন। তখন আমার আবার বইটার কথা মনেপড়ে গেল। কিন্তু ততদিনে আমি বইটা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। এইবার অনলাইনে খুঁজে একটা সাইট থেকে বইটা নামিয়েই পড়তে শুরু করলাম। অফিসের কাজকে ফাঁকি দিয়ে বাকী অংশ একবারেই শেষ করে ফেললাম। যদিও আগের বইটা ছিল ২০১৫ সালের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ আর অনলাইনেরটা হচ্ছে ২০১৪ সালের প্রথম সংস্করণ। তাই ঘটনার ধারাবাহিকতা মিলাতে একটু সময় লেগেছিল। অনলাইন সংস্করণটা শেষ করে ভাবলাম এই বইটা নিয়ে কিছু একটা অবশ্যই লেখা উচিৎ। তাই লজ্জা ভূলে আবার নাজমুল ভাই সন্ধ্যা ভাবির কাছ থেকে বইটা ধার নিয়ে পড়তে বসলাম।
পুরো বইটাকে আমি মূলতা তিনটা অংশে ভাগ করেছি। প্রথম অংশ ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর জন্ম থেকে ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত বেড়ে ওঠা এবং জীবন সংগ্রামের দিনলিপি। দ্বিতীয় অংশটা ১৯৭১ সালের দিনলিপি আর শেষের অংশটা হাজারো অপবাদ মাথায় নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে উনার জীবন সংগ্রামের দিনলিপি। অবশ্য দিনলিপি না বলে গল্প বলাই শ্রেয় কারণ উনি দিন তারিখ উল্লখ করে ঘটনার বিবরণ লিখেন নাই এবং সেটা উনি উনার লেখাতেই অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেনঃ “লিখতে লিখতে যেন আমি কোথাও খেই হারিয়ে ফেলি। তাই মাঝে-মাঝে প্রসঙ্গ থেকে বহুদূর ভাবনায় চলে যাই।”
বইটার প্রথম লাইনটা এমনঃ “আমি অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়ে।” এরপর একেবারে ধারাবাহিকভাবে উনি উনার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের গল্প থেকে শুরু করে বিবাহ এবং সন্তানধারণের গল্প বলে গেছেন। এই অংশটা পড়লে যে কেউ খুবই সহজে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন মেয়ের মনের ভাবনাকে জানতে পারবেন সেইসাথে পরিবার সমাজের সাথে কি পরিমাণ যুদ্ধ করে তাকে বেড়ে উঠতে হয় সেই ব্যাপারে ধারনা পাবেন। যদিও এটা ১৯৭১ পূর্ববর্তি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্রের সাথে কেন জানি মিলে যায়। তাই একজন সচেতন পাঠক খুব সহজেই লেখাগুলোকে নিজের সাথে রিলেট করতে পারবেন। এই অংশে একদিকে যেমন আছে দুরন্ত শৈশব কৈশরের ঘটনার বর্ণনা অপরদিকে আছে বয়সের সাথে ব্যক্তিত্বের মধ্যে দৃঢ়তার প্রকাশ।
শৈশব কৈশোরের নানা রঙিন ভাবনার বর্ণনা আছে বইটাতে। কাউকে উদ্দেশ্য করে অজানা অচেনা কিশোরের জানালায় প্রতিদিন ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখার ঘটনা যেটা একজন কিশোরির মনের চিরায়ত ভাবনার প্রতীক। আবার শত আদরের মধ্যেও নানু বাড়িতে নিজেকে ছোট মনেকরা। কেন একজন বাবা একটু সংসারি হয়ে তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটা আলাদা বাসায় না থেকে তার ছেলেমেয়েকে অন্যের বাড়িতে পাঠায় যদিও সেটা একান্ত আপনজনেরই বাড়ি। তবুও কিশোরী মনে এই অপারগতার জন্য আছে অপ্রকাশিত ক্রোধের বিবরণ। এছাড়াও একজন মেয়ে কিভাবে পরিবারে সমাজে নিগৃহীত হয় তার বিবরণ। শুধুমাত্র মেয়ে হবার কারণে পুরুষদের কাছ থেকেও পাওয়া বেশ কিছু আচরণ কিভাবে তাঁকে মর্মাহত করেছে আছে তার বিবরণ। এই অংশটুকু পাঠে বাংলাদেশের সমাজে একজন মেয়ের নিরলস সংগ্রামের ছবিই ফুটে উঠবে পাঠকের মনে।
এরপর আসে ১৯৭১ সাল। যে বছরটা উনার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় সেই সাথে বাংলাদেশেরও অন্ধকার অধ্যায় তার বিবরণ। ১৯৭১ সালের বিবরণের শুরুতেই উনি লিখেছেনঃ “এমনি করে যখন দিনগুলো কেটে যাচ্ছে, এমনই সময় এলো ১৯৭১। ব্যক্তিগত টানাপড়েনে বুঝে উঠতে পারছিলাম না ১৯৭১ সালের সূচনা মুহুর্তে, এ বছর আমার ভাগ্যে কি আছে।” এটা যেন বাংলাদেশেরই স্বগতোক্তি। কি ঘটতে চলেছে কেউই পরিষ্কার করে কিছু জানে না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা কেমন ছিল সেটার উনার বর্ণনা থেকে কিছটা ধারণা পাওয়া যাবে। কয়েকটা অংশ আমি এখানে তুলে ধরলাম।
“বিয়ার ভাই এসে আমার মাকে বললেন, ফেরদৌসী যদি কোথাও না যায়, আমার বলার কিছু নাই। কিন্তু আমাকে তো আত্মগোপন করতে হবে। বিহারিরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেদিন বোমা তৈরির কয়েকটি ছেলেকে বিহারিরা মেরে ফেলেছে। আমি তো থাকতে পারব না। আপনারা কোথায় যাবেন, বলেন আমি দিয়ে এসে চলে যাব। কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলতে বলতে সহসা বিয়ার ভাই কথা থামিয়ে বলেন, দেখেন মহা সড়কের পথ বেয়ে কিভাবে আর্মি বোঝায় ট্রাক চলে যাচ্ছে। কিছু গাড়ি পাস করে চলে যাবার পর আমরা গাড়িগুলো গুণতে থাকি। সাত আটটা বোঝাই আর্মি ট্রাক চলে যাবার পর আমরা যখন থেকে গুনলাম তখন থেকে ১২০ট্রাক বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র আর আর্মি ট্রাক পাস করে গেল।”
“একটু পড়ে দুপুর হবে। হঠাৎ দেখতে পাই তিনটি আর্মি বোঝাই গাড়ি রাজাকার মতিউল্লাহর নেতৃত্বে আমাদের বাড়ির চারপাশে বারবার ঘুরছে। আমি এই গাড়ির গতিবিধির ভয়াবহতা বুঝে ওঠার আগেই বিয়ার ভাই ঝটপট জানালা বন্ধ করে খাটের নিচে লুকিয়ে যান। বলেন, কী ভুলটা করলে তোমরা! আজ আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। একথা বলতে না বলতে গাড়ির বহরটি মুনশী বাড়িতে থামল। আমাদের বাড়ির সামনের বাড়ি। পরিবারের সব সদস্যরা আওয়ামী লীগ করে। এই অপরাধে ওদের বাড়ির ১৪ জন সদস্যকে আমাদের চোখের সামনে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলে চলে যায়। জানালার ফাঁক দিয়ে আমরা সবই দেখলাম। ৭ এপ্রিলের সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সে যে কী মর্মান্তিক! স্বচক্ষে দেখেছি। এরপরে ওরা আমাদের বাড়িটা বারবার ঘুরে ঘুরে দেখছিল। কোনো জামা-কাপড় বাইরে মেলা থাকলে, আর রক্ষা ছিল না।”
“ওই দেখেন আপনার পায়ের কাছে কি? মুহুর্তে চেয়ে দেখি গত ৭ এপ্রিল যে ভয়াবহ ব্রাশ ফায়ার করে মুনশী বাড়িতে ১৪ জনকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদেরই লাশের একটি বড় অংশ খাদক শেয়াল রেল ক্রসিং-এ টেনে নিয়ে এসে আরামে ভক্ষণ করছে। শেয়ালের সঙ্গী কুকুর ও শকুন একযোগে খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। এ দৃশ্য আমাকেও যেন কেমন অমানুষ করে তুলল। হঠাৎ মনে হলো অনেক শেয়ালই বোধহয় সারা বাংলাদেশে এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যারা আমাকে, মাকে খাচ্ছে, স্বজনকে খাচ্ছে, এদেশের সকল শিশু আবালবৃদ্ধবনিতাকে ভক্ষণ করছে। ”
“মনে মনে ভাবি দুঃসময়ে, দুর্যগে বেঁচে আছি। বুকের মধ্যে সমুদ্র পরিমাণ দুঃস্বপ্ন। এর মধ্যে একদিন জেগে বসে থেকে, সহসা শুনতে পাই, বাচাও! বাচাও! কার করুণ আকুতি? শোবার ঘরের খাটের সাথেই জানালা দিয়ে দেখা যায় ভৈরব নদী। নদীর পাড়ে দু-একটা বড় নৌকা। বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। বার্জ। দুটো বিশাল লরি দাঁড়ানো। কিছু মানুষের মুখ কালো কাপড়ে বাঁধা। তারা ট্রাক থেকে মুখ বাঁধা লোকগুলোকে পাট কাটার মেশিনে মাথা ঢুকিয়ে ঘ্যাচাং করে দ্বিখন্ডিত করে মৃতদেহ ও মাথা নদীতে ফেলে দিচ্ছে। এমন দু-তিনটি হত্যাকাণ্ড দেখে খাটের মধ্যে মাথা লুকালাম। মনে হলো ওরা বোধহয় আমাকেও দেখে ফেলেছে।”
“এরপরে ওরা আমাকে বন্দি শিবিরে পাঠিয়ে দেয়। ওখানকার আবহাওয়া দেখেই আমার বুঝতে বাকি রইলো না, এবারে আমার মৃত্যু ছাড়া আর রক্ষা নেই। একটি লম্বা ব্যারাকের মতো। সেখানে গ্রামের অনেক নাড়িকে এনে নির্যাতন করা হচ্ছে। অত্যাচারীরা সবাই জওয়ান। এতদিনে জওয়ানদের হাতে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। বীভৎস এ দৃশ্য আমাকে হতবাক করে দেয়। ইতিমধ্যে হতাশ হয়ে, মনকে প্রবোধ দিয়েছি, হয় মুক্তি না হয় মৃত্যু। আমার দেহের কোথাও হাত দেওয়া যাচ্ছে না এত ব্যাথা।
“বাসে ফিরে আসছিলাম। নোয়াপাড়া থেকে রাজাকার সাবদুল্লা উঠেছে সালোয়ার কামিজ পরা। শহীদ মিনারের দিকে তর্জনী তুলে বলে, ওই যে শহীদ মিনার, চেয়ে দেখেন, দু’টি মন্ডু এইমাত্র কেটে ঝুলিয়েছি, আরো দুটো মন্ডু ঝুলিয়ে দিলে বেশ মানানসই হবে। আমি শহীদ মিনারের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখতে পাই সত্যিই সেই দিন দুপুরে তরতাজা দুটি মানুষের মন্ডু ঝুলছে। লম্বা চুল মহিলার মন্ডুটি আমি স্পষ্টই দেখতে পেলাম। অন্যটি আবছাভাবে দেখেছিলাম হয়তোবা পুরুষ কিংবা নারী। পথে ঘাটে চলতে ফিরতে এমন দৃশ্য! ছিল অতি স্বাভাবিক। কী ছিল সেই দিনগুলো বোঝানো খুব কঠিন।”
মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষেরদিকের বর্ণনা দিতে যেয়ে লিখেছেনঃ “হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ওকে (রাজাকার সাবদুল্লাহ) ধরার জন্য ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। সে মারাই যাবে, সেই মৃত্যুর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আমি (বিয়ার ভাই) অর পিঠে একটু হাত দিলাম। এতবড় হতভাগ্য মানুষ আর নাই। এ কথা বল শেষ হলে আমি উপরে উঠে আসি। কিছুক্ষণ পর গেটের কাছে ভীষণ চিৎকার আর হট্টগোলের আওয়াজ। কিছু না বুঝেই আমি নিচে নেমে এসে গেটের কাছে বিয়ার ভাইকে দাঁড়াতে দেখে ওর কাছে এগিয়ে যেতেই দেখতে পাই এক বীভৎস দৃশ্য। লক্ষ্য করলাম একটি মানুষকে কারা যেন দু’দিক থেকে টানাটানি করছে। বিয়ার ভাই বললেন, তুমি এ দৃশ্য দেখো না। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিয়ার ভাইকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখতে পেলাম এক মর্মান্তিক দৃশ্য। হত্যাকারী রাজাকার কমান্ডার সাবদুল্লাহ মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। হাজার হাজার মানুষ তাঁকে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। সেদিন ১৬ ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস।”
আমি খুবই সচেনভাবে উনার নিজের উপর চালানো পাকিস্তানি আর্মির এবং অন্যদের অত্যাচারের ঘটনাগুলো এড়িয়ে গেলাম। কারণটা হচ্ছে আমি ঐ ঘটনাগুলো একবারই পড়েছি। দ্বিতীয়বার পড়ার মত আমার সাহস নাই। ২৫শে মার্চ রাত থেকে ১৬ ডিসেম্বরের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিশাল এবং বহুমাত্রিক ভয়াবহতার একটা ধারণা পাওয়া যায়। একজন সুস্থ্য মস্তিস্কের মানুষের পক্ষে খুব সহজেই এই ঘটনাগুলো পড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার চিত্র কল্পনা করে নেয়া সম্ভব যদিও ঘটনাগুলোর সবই ছিল নির্মম বাস্তব।
বইটার তৃতীয় অংশটাতে আছে একেবারে প্রতিকূল পরিবেশে সর্বস্ব খোয়ানো একজন মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা। সেই সাথে প্রাসংজ্ঞিকভাবেই এসে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা, শাসকদের স্বরূপ, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের বিচারের প্রক্রিয়া। সাথেসাথেই উঠে এসেছে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর ভাস্কর হয়ে ওঠার বর্ণনা। এসেছে শিল্পী এস এম সুলতানের জীবনীর কিছু অংশ। সব মিলিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের কিছু বাস্তব বিবরণ। এবার আমরা সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই।
“লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজপথে নেমেছে। কোন কোন বাড়িতে কান্নার রোল, মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া স্বামী বা সন্তান ফিরে আসে নি। আমার অন্তরে রক্তক্ষরণ চলছে। আমাকে অনেকবার অহর্নিশ আর্মি ফাঁড়িতে যাওয়া-আসা করতে দেখা গেছে। এজন্য গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে আমাকে যুদ্ধ সহযোগী হিসেবে গণ্য করা হবে। এর চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। মনে মনে ধরে নিলাম এবারে আমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমি কিছু ঘটাবো, সিদ্ধান্ত নিলাম আবার ভাবলাম দুর্নাম মাথায় নিয়ে আমি সমাজভয়ে পালিয়ে যাবো চিরদিনের জন্য, তা হতে পারবে না সমাজকে প্রত্যাখ্যান করে সমাজ শৃংখলে প্রচন্ড আঘাত করে বেঁচে থাকার চেষ্টাতে আমার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মিত্যে আর্তনাদ। আমার নিজেকে রক্ষা করার মতো কোন সম্বল ছিল না। না ছিল বয়সের প্রাচুর্য্য, না ছিল সামাজিক শক্তি। ছিল না আর্থিক বল। না ছিল শিক্ষার মান। কি নিয়ে আমি ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলব। অতএব নয় মাসের নারকীয় যুদ্ধ পরিণতির ভার আমার উপরে ধ্বসে পরেছিল।”
“১৬ ডিসেম্বর দুপুর একটা। বিয়ার ভাই এসে বললে চলো তোমাকে একটা দৃশ্য দেখিয়ে আনি। ওর সাথে আমি গাড়িতে উঠলাম। সার্কিট হাউসে পাকিস্তানি সামরিক অফিসারদের আত্মসমর্পন শুরু হয়েছে, আমরা সারেন্ডার দেখলাম। তারপর বিয়ার গাড়ি ঘুড়িয়ে আমাকে গল্লামারি রেডিও স্টেশনের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পোড়ামাটি ণীতি প্রয়োগ করে শেষ মুহুর্তে লেকের দু’ধারে অসংখ্য মানুষ ফেলেছে। সদ্য হত্যাকৃত লাশগুলো একের পর এক মাইল জুড়ে পড়ে আছে। পাটের ক্ষেতে বাতাসে দুলে যায় শুধুই লাশ। কত যে লাশ তা গণনা করার বা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। আমার কাছে ও যেন খুব কঠিন দৃশ্য মনে হচ্ছিল না। গত নয় মাস ধরে আমি প্রতিদিনই কিছু ছিন্নভিন্ন বীভৎস শরীরের অংশবিশেষ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। সেই সব খন্ড বিখন্ড সামগ্রীর যোগফলই আজকের স্বাধীনতা। মহান বিজয়।
সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্রায়। পিছন ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পাই একতলা বাড়ির সমান উচ্চতায় দুটি পাহাড়ের মত স্তম্ভ, যার উপর থেকে নিচ পাদদেশ পর্যন্ত কঙ্কাল, মাথার খুলি, হাত, বুকের পাঁজরের দৃশ্যমান পাহাড়। গত ন’মাসের অপকীর্তি বিশেষ। বুকটা কেমন ভারী হয়ে উঠলো। বিয়ার ভাইকে সন্ধ্যার অন্ধকারে বড়ই আপন মনে হয়েছিল। সে বলল, এখানে আর দেরি করা যাবে না। কেননা জায়গাটি বড়ই নির্জন। হত্যাকারী এখনো আশেপাশে আছে। এত হাজার হাজার লাশ শেষ মুহুর্তে এল কোথা থেকে? চলো, এখান থেকে।
সাঙ্গ হলো বেলা। গত ন’মাসের বিচিত্র দুঃসহ ঘটনা। এই বিস্তীর্ণ বন্দর নগরী যেন পোড়ামাটির নীল নাশকতার কবলে পরেছিল শেষ মুহুর্তে।”
এরপর আমরা বইটার একেবারে শেষের পৃষ্ঠায় ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণীর শিল্পী মনের পরিচয় পাই। একজন মানুষ এত অত্যাচার অনাচার সহ্য করার পরও যখন এই কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারেন তখন তার জন্য শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসেঃ “কবিগুরু কিংবা জীবনান্দ দাশের নায়িকা হয়ে ওঁদের কবিতায় প্রিয়ভাষিনী হয়ে ফিরে আসবো। এই সোনার বাংলায়। দীপ্তিময় বীরাঙ্গনা মায়ের মর্যাদা আর আত্মত্যাগী লাখো শহীদের ভালোবাসা আর আত্মত্যাগের এই স্বাধীন বাংলায় ফিরে বার বারই ফিরে আসবো। মায়ের আঁচলে সবুজ পতাকা নিয়ে ফিরে আসবো। লাখো বীরাঙ্গনা মায়ের জন্য কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হব আজীবন। কারণ আমি বাঙালি, আমার দেশ বাংলাদেশ।” একাহ্নে উল্লেখ্য উনি বইটি উৎসর্গ করেছেন “১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং নির্যাতিতা মা-বোনদের স্মরণে”।
মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বই বিষয়ে আমার একটা নিজস্ব মতামত হচ্ছে এই বইগুলোর সরকারীভাবে তালিকা করা জরুরি। সেই বইগুলো শুধু বাংলাতে না বরং সেগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা দরকার বিশেষকরে ইংরেজিতে অনুবাদ করা এখন সময়ের দাবি। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের একটা বিশাল অংশ দেশে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ছে আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিদের নতুন প্রজন্মও অন্য ভাষাতে শিক্ষিত হচ্ছে। ইংরেজিতে এই বইগুলো অনুবাদ হলে অন্ততপক্ষে তারা সেটা পড়ার সুযোগ পাবে এবং সামান্যতম হলেও অন্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করবে। সম্প্রতি আমি অনলাইনে আমার মেয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধের বই খুজতে যেয়ে বাংলাদেশি লেখকদের মাত্র দুটি বই পেয়েছি ইংরেজিতে। একটি হচ্ছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের “রাশেদ মাই ফ্রেন্ড” আর অন্যটি হচ্ছে আনিসুল হকের “ফ্রিডম ফাইটার’স মম”। তাই ভাবছি ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর এই বইটা ইংরেজিতে অনুবাদ করার কাজে হাত দিব যাতেকরে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম এই বইটা পড়ে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বিশালতার একটা চাক্ষুষ ধারণা পায়।
মুক্তিযুদ্ধের বই পড়া নিয়েও আমার একটা নিজস্ব মতামত হচ্ছে আমাদের সরকার তো বিভিন্ন খাতে কত টাকায় ব্যায় করে। তার থেকে যদি একটু বাচিয়ে শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের কিছু বই প্রত্যেক পরিবারের জন্য এক কপি করে দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা পরিবারের সকল সদস্য না হলেও নতুন প্রজন্ম খুব সহজেই মুক্তিযুদ্ধের একটা ধারণা পেতে পারে। পরিশেষে একটা কথায় বলতে চাই আমরা যতভাবেই অস্বীকার করার চেষ্টা করি না কেন মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোনের জীবন-সম্ভ্রমের বিনিময়েই আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছিলাম। যারফলে এখন আমরা বিশ্বের বুকে গর্বিত একটা দেশ। তাই আপনি যে দল-মতের লোকই হোন না কেন মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে না পারেন অন্ততপক্ষে অসম্মান জানানোর অধিকার আমার আপনার নেই। তাহলে যে নিজের আত্ম-পরিচয়ই প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
মো: ইয়াকুব আলী
বিষয়: মোঃ ইয়াকুব আলী

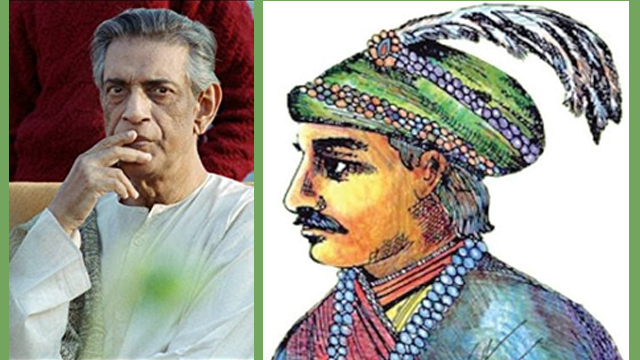
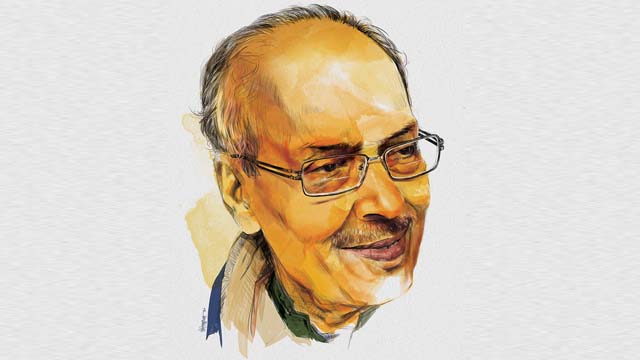



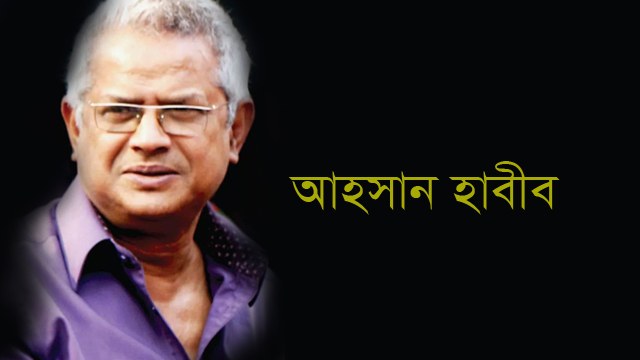


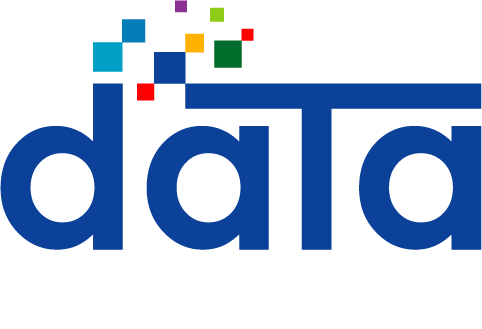
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: