এলিস মুনরোঃ চেনা জীবনের গল্প রচনায় যিনি অনন্য : ড. আফরোজা পারভীন
প্রকাশিত:
৫ নভেম্বর ২০২০ ২১:৪৬
আপডেট:
৫ নভেম্বর ২০২০ ২২:০৩
অ্যালিস অ্যান মানরো (অষরপব অহহ গঁহৎড়; জুলাই, ১৯৩১) কানাডার বিশিষ্ট ছোটগল্প লেখক। কানাডার কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল নাম ও যশস্বী ব্যক্তিত্ব। দ্য নিউ ইয়রকার, দি আটলান্টিক মান্থলি, দ্য প্যারিস রিভিউ-এর মতো প্রসিদ্ধ সাহিত্য পত্রিকার নিয়মিত লেখক; কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের একাধিক সাহিত্য-সম্মাননায় সংবর্ধিত এই ছোটগল্পকার কানাডার সাহিত্যজগতের মধ্যমণি।
তিনি তাঁর সাহিত্য কীর্তির জন্য ২০১৩ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এর আগে ২০০৯ সালে ম্যান বুকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি গদ্যের জন্য তিনবার কানাডার গভর্নর জেনারেল পুরস্কার পেয়েছেন।
তিনি তার গল্পে দক্ষিণ-পশ্চিম অন্টারিও এলাকা, স্কচ-আইরিশ বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন তাদের জীবনের প্রাত্যহিকতা। তুলে এনেছেন তাদের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, যার কোনো কোনোটির মধ্যে বিরাজিত অপার মহিমা। তাঁর লেখায় উপমার ব্যবহার অসাধারণ। বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে লেখেন তিনি। বিধৃত করেন যে জনজীবন সে জীবনের অর্থনৈতিক মানসিক মনস্তাত্বিক কোন দিকই বাদ যায় না তাঁর লেখা থেকে। তিনি তুলে ধরেন আপাত অতি সাধারণ ব্যক্তিদের গভীর ও জটিল মনোগত দিক ।
মুনরোর জন্ম ১৯৩১ সালে। কানাডার অন্টারিওর ক্লিনটন নামক ছোট শহরের কাছে। বাবা ছিলেন শীতবস্ত্রে ব্যবহৃত মূল্যবান লোম ও পশম যেসব পশু থেকে পাওয়া যায় সেসব পশু খামারের মালিক। মা ছিলেন শিক্ষিকা। মাত্র ১১ বছর বয়সেই মুনরো ঠিক করে ফেলেন, বড় হয়ে একজন লেখকই হবেন। সে মতোই এগিয়েছে সবকিছু। নিজের পেশা নিয়ে নিসংশয় ছিলেন। কখনো দ্বিধা সংকোচে ভোগেননি। এক সাক্ষাৎকারে মুনরো তাই বলেছেন, ‘আমি মনে করেছিলাম, লেখালেখি করেই আমি কেবল সফল হতে পারি। কেননা, আমার মধ্যে অন্য কোনো গুণ ছিল না।’ তিনি আরো বলেছেন, ‘আমি সত্যিই বুদ্ধিজীবী ধরনের কেউ নই, বরং একজন ভালো গৃহবধূ।’ শেষাংশটুকু যে তাঁর বিনয় এটা বুঝতে কোনোই অসুবিধা হবার কথা নয় কারো। তবে তিনি গৃহবধু, মা সবই। সে দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন সুচারুভাবে।
এলিস নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর হাতে কোনো টাকা পয়সা ছিল না। জীবনে কঠোর সংগ্রাম করে সাফল্য অর্জন করেছেন। ওয়েস্টার্ন অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতকের ছাত্রী ছিলেন। নানা ধরনের চাকরি করেছেন পড়ার খরচ জোগাতে। ১৯৫০ সাল, তখনো তিনি ছাত্রী, তাঁর গল্প ছাপা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন দু বছরের জন্য বৃত্তি দেয়া হতো। এরপর তাঁর আর পড়াশুনার সুযোগ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দ্বিতীয় বর্ষেই তিনি বিয়ে করেন। তিনি যখন বিয়ে করেন তখন তাঁর বয় বিশ।১৯৫১- তে বিয়ে করেন সহপাঠী জেমস মুনরোকে। স্বামী ও এলিস মিলে বইয়ের দোকান দেন। এই দোকানই ছিল সংসারের আয়ের উৎস। এই সংসারে আসে চার কন্যা সন্তান।
তাঁর ভাষায়, ‘বিয়ে করা একটা দারুণ ব্যাপার, একটা বিরাট অভিযান, অভিযাত্রা। আমরা দেশের ভেতরেই দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাই। আমার বিশ আর তাঁর বাইশ বছর বয়স। আমরা এরই মধ্যে নিজেদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মতো করে তৈরি করে ফেলি। আমরা একটি বাড়ি কেনার কথা ভাবি এবং ভাবি একটি সন্তান নেওয়ার কথা। এ জিনিসগুলো তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। প্রথম সন্তান হয় আমার একুশ বছর বয়সে।’
অন্তঃসত্তাকালে পুরো সময়টাতেই তিনি মরিয়া হয়ে লিখতেন। কেন না তার মনে হতো এর পরে আর তিনি লিখতে পারবেন না । চারবার অন্তঃসত্তা হয়েছেন তিনি। প্রতিটি অন্তঃসত্তা অবস্থাই তাঁকে শক্তির জোগান দিত, যাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি বিরাট একটা কিছু শেষ করতে পারেন। একজন নিবেদিত লেখকের পক্ষেই এতটা নিষ্ঠ হওয়া সম্ভব। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে তিনি যখন লিখতেন তখন তাঁর মেয়েটি দোলনা থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। বাচ্চারা স্কুলে গেলেই তিনি লিখতে শুরু করতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেন তিনি। তাঁর স্বামী এবং তাঁর একটি বইয়ের দোকান ছিল। দোকানের কাজ ছাড়াও দুপুর পর্যন্ত বাড়িতে কাজ করতেন তিনি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে লিখতেন। পরে প্রতিদিন তাকে দোকানে যেতে হতো না। সবাই লাঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত লিখতেন। লাঞ্চ সেরে তারা চলে গেলে আমি আবার লিখতেন। তারপর আবার বাড়ির কাজ। এসব করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত।
মেয়েরা দুপুর ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ঘুমাতো। ওই সময়ও তিনি লিখতেন। তিনি প্রায়ই রাত পর ১টা পর্যন্ত কাজ করতেন। আবার সকাল ৬ টাতেই উঠে যেতেন। এত কাজ করতেন যে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হতো বুঝি মরেই যাবেন বা আমার হার্ট অ্যাটাক হবে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ঊনচল্লিশ¬। অথচ অজস্র কাজ তাঁর মাথায় চেপে থাকত।
প্রচুর নোটবুক আছে তাঁর। নোটবুকগুলোতে তিনি সাধারণত যেকোনো জিনিস টুকে রাখেন। তিনি অন্যদের মত নন। ‘অন্যরা আশীর্বাদপুষ্ট, তরতর করে ওপরে উঠে যায়। আমি যা কিছুই করতে চেষ্টা করি না কেন, আমার জন্য অত সহজে কিছুই হয় না।’ একথা এলিস মনিরোর।
দশ বছর পর জেমসের সাথে বিচ্ছেদ হয় ১৯৭২ সালে। অতঃপর ওয়েস্টার্ন অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃজনশীল লেখার শিক্ষকতা করেন কিছুদিন। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরে তাঁকে ডি-লিট সম্মানে বরণ করেছিল। সেটা ১৯৭৬ সাল। সেই বছর জেরাল্ড ফ্রেমলিনকে বিয়ে করেন। জেরাল্ডের সাথে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। পেশায় জেরাল্ড ছিলেন ভূগোলবিদ, মানচিত্রকার। বিয়ের পর অন্টারিওর ছোট শহর ক্লিনটনের কাছে জেরাল্ডের খামার বাড়িতে তাঁরা নতুন সংসার পাতেন। এই বাড়িতে ৮৮ বছর বয়সে ২০১৩ এর ১৭ এপ্রিল জেরাল্ড ফ্রেমলিনের মৃত্যু হয়। এখনও তিনি ওই বাড়িতেই আছেন। এলিস নিজে দুরারোগ্য ব্যাধির জটিলতায় আক্রান্ত। ২০০৯ সালের টরন্টো শহরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এলিস তাঁর হৃদপিন্ডের বাইপাস অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি এবং ক্যানসার-চিকিৎসা গ্রহণের কথা জানিয়েছিলেন।
ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াই ছিল তাঁর জীবন। তিনি বইয়ের মধ্যেই বাস করতেন। ফ্ল্যানারি ও কনর, ক্যাথারিন এন পোটার, কারসন ম্যাক কালার্স, ইউডোরা ওয়েলটি ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখকের তালিকায়। ভালোবাসেন জাদুবাস্তবতার রীতিতে লেখা উপন্যাস। উইলিয়াম ম্যাক্সওয়েলের উপন্যাস সো লং, সি ইউ টুমোরো, মার্কেজের ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অব সলিটিউড তাঁর প্রিয়। ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অব সলিটিউকে বলেছেন অনন্য, তবে আদর্শ হিসেবে নেয়ার মতো নয়।
মুনরোর মায়ের দিকের আত্মীয়রা শহরবাসী। বাবার জীবনজীবিকা গ্রামকেন্দ্রিক। মন-মানসিকতায়, অভিরুচিতে, জীবনযাপন পদ্ধতিতে দুই পরিবারে ছিল পার্থক্য। ছিল দ্বন্দ্ব। শহুরে শিক্ষাভিমানী ভদ্রসমাজের মানুষরা গ্রামের মানুষজনকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। এই দ্বন্দ্ব এলিস মুনরো আশ্চর্য কুশলতায় তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।এ ক্ষেত্রে গল্পের উপাদান এসেছে তাঁর কৈশোর- যৌবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। খুব কাছে থেকে দেখা, নিবিড় অন্তরঙ্গভাবে জানা কানাডার বিশেষ অঞ্চল অন্টারিওর হিউরন কাউন্টি, যেখান পৈতৃক বাড়ি এবং দ্বিতীয় স্বামী গ্যারি ফ্রেমলি¬নের বাড়ি, এই ভূখন্ডই এলিস মুনরোর প্রিয় স্থান। এই ভূভাগের প্রেক্ষাপটে গল্পগুলি রচিত। লরেন্সের উপন্যাসে যেমন নটিংহাম, হার্ডির উপন্যাসে যেমন ওয়েসেক্স, ফকনার ও ফ্ল্যানারি ও কনরের উপন্যাসে আমেরিকার মধ্য দক্ষিণাঞ্চল, সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে যেমন জলেশ্বরীতলা, হুমায়ুন আহমেদের গল্পে যেমন সুখী নীলগঞ্জ মুনরোর গল্পে তেমনই বারবার ঘটনাস্থান হিসেবে চিত্রিত হয়েছে, কানাডার অন্টারিওর হিউরন কাউন্টির নিসর্গ। ছোট শহর ও গ্রাম মেশানো অঞ্চলটি এলিস মুনরোর বহু গল্পে অবিস্মরণীয়তা পেয়েছে। রক্ষণশীল সংকীর্ণ মানসিকতার সমাজে একটি মেয়ের বেড়ে ওঠা, পরিবার ও সমাজের সাথে সংঘাত- এই বিষয়টি তাঁর অনেক গল্পের উপজীব্য। তাঁর গল্পে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে গল্পের নারীরা শক্তিমত্ত, বহুমাত্রিক, বহুরৈখিক তাদের মানসিকতা। তাঁর গল্পে কর্তৃত্বপরায়ণা অনেক মাসি, দিদিমার দেখা মেলে। আবার পাই অনেক মাকে। বিভিন্ন রকম বিভিন্ন ধরণের মা। পাই পরিণত বয়সের বৃদ্ধা-মধ্যবয়সী নিঃসঙ্গ নারীদের আলেখ্য, যাদের সাধারণ, আটপৌরে, আপাততুচ্ছ দিনানুদৈনিক জীবন গভীর কোনো উপলব্ধি বা বোধের হঠাৎ উদ্ভাসনে অর্থময় হয়ে যায়। এলিস মুনরোর গল্পের চরিত্রদের চেতনার জগৎ দীপ্যমান হয়ে ওঠে যাদেও কারণে।
মুনরোর অনেক গল্পে কাহিনি নিতান্ত স্বল্প বা গৌণ। তবে বোধের জায়গাটি বিশেষ বা বিশাল। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে, সমালোচকরা তাঁকে রাশিয়ার গল্পকার আন্তন চেখভের সাথে তুলনা করেছেন।
মুনরোর জীবনে আছে রোগযন্ত্রণার নির্মম অভিজ্ঞতা, অনেক আপনজন, নিকটাত্মীয়ের (পিতা, মাতা, কন্যা, স্বামী ও অন্যান্য) মৃত্যুর নিদারুণ আঘাত। এতসব কিছুর মধ্য দিয়ে জীবনের এতটা বছর পার করে এসেছেন তিনি। আঘাত, শোক, প্রিয় মানুষের বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর রচনায় বারবার। তাঁর জীবন ও রচনার এই বৈশিষ্ট্যকে আলোকপাত করে অনেক সমালোচক গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন।
মুনরোর বেশির ভাগ গল্পে উঠে এসেছে কানাডার গ্রামাঞ্চলের পরিবেশ। অন্য বড় লেখকদের মতো তিনি বিশ্বভ্রমণে বের হননি। স্বাভাবিকভাবেই নিজের চারপাশের গন্ডির বাইরের বিষয় নিয়ে তাঁর লেখালেখিও কম।
কানাডার পুরুষ লেখকদের বরাবর এড়িয়ে চলেছেন তিনি। তিনি মনে করেন, সাহিত্যিকদের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ সংসর্গে হয়তো তাঁর লেখার ক্ষতিই হতো। তাঁরা হয়ত তাঁকে বক্রোক্তি করত, হয়ত আক্রমণে করত। তাতে তাঁর আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগত। তিনি বেছে নিয়েছেন নিভৃতি। মমতা দিয়ে লিখেছেন নারীর চোখে দেখা নারীর কথা। প্রান্তজনের কথা। নারীর জীবনের নানা ধাপ, কুমারী, , দাম্পত্য, পারিবারিক, সামাজিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার কথা। তিনি লিখেছেন সুক্ষাতিসূক্ষ ঘটনা যা অন্যের নজর এড়িয়ে যায়। এখানেই তিনি আলাদা, বিশেষ। নারীর নারীত্ব, মাতৃত্ব, প্রেমিকা, স্ত্রীর ভূমিকায় তিনি চারপাশের মানুষের ছবিই এঁকেছেন। সাধারণত যারা থাকে উপিক্ষিত। তারাই জায়গা পেয়েছে তাঁর কলমে। এই যে সাধারণ বিষয় নিয়ে লেখা এর বদৌলতে যে সম্মাননা ও স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন, তা তাঁর নিজ দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মূলধারার অন্যতম প্রধান সাহিত্য রচয়িতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি সাহিত্যে প্রথম কানাডা-অধিবাসী নোবেল বিজয়ী। আমেরিকার, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া থেকে এক ডজনের বেশি সাহিত্য পুরস্কারে হয়েছেন সম্মানিত।
মুনরোকে ‘সমকালীন ছোটগল্পের মাস্টার’ অভিহিত করে নোবেল কমিটি বলেছে, ‘তিনি খুব সুন্দর করে গুছিয়ে গল্প বলতে পারেন। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট ও বাস্তববাদী। অনেকেই তাঁকে কানাডার চেখভ বলে থাকেন।’ ৮২ বছর বয়সী মুনরোর কাছে যখন নোবেল জয়ের খবর পৌঁছে তখন তিনি ‘চরম বিস্মিত’ হন। তিনি বলেন, ‘জানতাম তালিকায় আমার নাম আছে। কিন্তু কখনো ভাবিনি যে আমিই জিতব।’
নোবেল কমিটি বলেছে, ‘তাঁর প্রায় সব গল্পের উপজীব্য ছোট কোনো শহরের প্রেক্ষাপট। এতে উঠে এসেছে সম্পর্ক ও নৈতিকতার টানাপোড়েন, যার সৃষ্টি এক প্রজন্মের সঙ্গে আরেক প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব থেকে।’
মুনরো নিজেও স্বীকার করেছেন সে কথা, ‘এখানকার পরিবেশের ভেতরেই জীবন-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমি বেড়ে উঠেছি। কাজেই এখানকার আবহ আমি যতটা গভীরভাবে অনুভব করতে পারি, অন্য কোনো নতুন জায়গা সম্পর্কে সেটা সম্ভব নয়।’
মুনরো গভর্নর জেনারেল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তিন তিনবার। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ড্যান্স অব দ্য হ্যাপি শেডস, ১৯৭৮ সালে হু ডু ইউ থিংক ইউ আর এবং ১৯৮৬ সালে দ্য প্রোগ্রেস অব লাভ বইয়ের জন্য। তিনি কানাডার সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কারও পেয়েছেন। ম্যান বুকার পুরস্কার পেয়েছেন ২০০৯ সালে দ্য বেয়ার কাম ওভার দ্য মাউন্টেন বইয়ের জন্য । তাঁর এই বই অবলম্বনে পরিচালক সারাহ পলি তৈরি করেছেন সিনেমা অ্যাওয়ে ফ্রম হার।
মুনরোর প্রকাশিত অন্যান্য ছোটগল্পের সংকলনের মধ্যে আছে লাইভস অব গার্লস অ্যান্ড উইম্যান-১৯৭১, সামথিং আই হ্যাভ বিন মিনিং টু টেল ইউ-১৯৭৪, দ্য মুনস অব জুপিটার-১৯৮২, ফ্রেন্ড অব মাই ইয়োথ-১৯৯০, ওপেন সিক্রেটস-১৯৯৪, দ্য লাভ অব আ গুড উইম্যান-১৯৯৮, হেটশিপ ফ্রেন্ডশিপ কোর্টশিপ লাভশিপ ম্যারিজ-২০০১, রানঅ্যাওয়ে-২০০৪, টু মাচ হ্যাপিনেস-২০০৯ এবং ডিয়ার লাইফ-২০১২।
এলিস মুনরো বছরের বেশির ভাগ সময় কাটান কানাডার অন্টারিও রাজ্যের ছোট্ট শহর ক্লিনটনে। মুনরোর ভাষ্যমতে, ফ্রেমলিন ওই বাড়িতেই জন্মেছিলেন। বাড়িটার পেছনে সুন্দর একটা উঠান আর একটা অদ্ভুত ফুলের বাগান আছে। মুনরো নিজে রান্না করেন। তাঁর খাবার ঘরের একদিকটায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, একপাশে একটা ছোট্ট টেবিলে একটা সেকেলে টাইপরাইটার। মুনরো ওই টাইপরাইটারে লেখেন।
মুনরো আর মুনরোর স্বামী দুজনই তাঁদের বর্তমান আবাসস্থল থেকে বিশ মাইলের ভেতরে বেড়ে উঠেছেন; আশপাশের প্রায় প্রতিটি বাড়ির ইতিহাস তাঁদের নখদর্পণে।
সৌজন্যে মুনরো অনন্য, রসবোধে পরিমিত। এত সব সম্মানজনক অর্জন সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠে সাহিত্যে নবাগতদের মতো অনিশ্চয়তা স্পষ্ট। তাঁর মাঝে বিখ্যাত লেখকসুলভ কোনো ঔদ্ধত্য বা উন্নাসিকতা নেই; তাঁকে দেখলে বিখ্যাত লেখক বলে মনেও হয় না। নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে কঠোর পরিশ্রম করলে যে কারো পক্ষে এমন লিখতে পারা সম্ভব। বস্তুত তাঁর লেখার সরলতা অত্যন্ত বিরল।
তিনি এখনও পুরোনো লেখাগুলো পড়েন, প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন। তিনি কখনই চান না এমন কোনো জটিল ভাষা ব্যবহার করতে যা পড়তে গিয়ে পাঠকরা হোঁচট খান। সহজ সরল ঝরঝরে ভাষাই তাঁর পছন্দ।
ছোট্ট একটা গন্ডি নিয়ে লিখেছেন তিনি। বলেছেনও তিনি ‘মূলধারা থেকে আমি এতটাই দূরে সরে থেকেছি যে আমি অনুধাবন করতে পেরেছি মেয়েরা পুরুষদের মতো এত সহজেই লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না, যেমন পারে না, নিচু শ্রেণির লোকজন।’
তিনি বলেছেন বটে কিন্তু সৃষ্টি করেছেন অমর কিছু লেখা। তাঁর চোখ গল্পটির শ্যাডির কথা যদি ভাবি সেখান মা মেয়ের যে জটিল আন্তসম্পর্ক দেখানো হয়েছে তা আমাদের চেনা জানা অনেক সংসারেই আছে। অথচ আমরা তা দেখেও দেখি না, বা বুঝি না। আমাদের মায়েরা তাদের আধিপত্যবাদ তাদের সন্তানের উপর চাপিয়ে দেন। এমন ভাব করেন, সন্তানের সবই যেন তার জানা। সন্তানের সব চাওযা পাওযা তার মুখস্থ। নিজের চাওয়াকে সন্তানের চাওয়া বলে চালিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। আবার সন্তান যদি অন্য কাউকে বেশি ভালবাসে সেটাও পছন্দ করেন না। এমন নয় যে পুরুষ নারীর ব্যাপার। পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে ভালবাসাও তারা পছন্দ করেন না। তারা চান সন্তান তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসবে, সে যাকে বলবে তাকেই ভালবাসবে। কিন্তু বাস্তব তো এমন নয়। এই অতি সূক্ষ্ম বিষয়টিকে সাগর সেঁচে ঝিনুকের মাঝে মুক্ত তুলে আনার মতো তুলে এনেছেন তিনি ‘চোখ’ গল্পে। এ গল্পে বোঝা যায় শ্যাডি মারা যাবার পর নিজেকে বিজয়ী মনে করছেন মা। কারণ তার মেয়েটি শ্যাডিকে খুব পছন্দ করত। মার মনে হয়েছিল মেয়েটি তাকে বা তার পর পর আসা দুই সন্তানের চেয়ে শ্যাডিকে বেশি পছন্দ করত। সেজন্য তিনি ইচ্ছে করে মেয়েকে শ্যাডির মৃতদেহ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং মেয়ের মনে হয়েছিল মার মুখে বিজয়ীর হাসি। শ্যাডির চোখের পাতা নড়ানো দিয়ে লেখক ইঙ্গিত করেছেন পুরো সমাজের কপটতার দিকে। এই ধরণের লেখার জন্য দৃষ্টি থাকার দরকার। বহৎ পরিসরে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই বা যাকে বরা হচ্ছে মূলধারা অর্থাৎ বড় বড় জায়গা বড় বড় ঘটনা সেসবেরও কোনো প্রয়োজন নেই। বা আমরা যদি তাঁর ‘মাউন্ট সিটি মন্টানা’ গল্পটি পড়ি তাহলে মুনরোর দেখার চোখ ও অনুভূতির সূক্ষ¥তা সম্পর্কে বুঝতে পারবো। স্টিভ গলির বয়স আট বছর । মা নেই বাবা ছন্নছাড়া। শ্রমিক, ভাড়ায় শ্রম দেয়। মদ খায় কিন্তু মাতাল হয় না। একটা কুঁড়েঘরে বাপ ছেলে একসাথে থাকে বটে কিন্তু কেউ কারো খবর রাখে না। এমনকি একজন আরেকজনের জন্য খাবারও বানায় না। স্টিভ গলি নিঁখোজ হয়। গ্রামের লোক প্রবল উৎসাহ আর উত্তেজনা নিয়ে তাঁকে খুঁজতে যায়। পানিতে ডুবে মারা যায় স্টিভ গলি। ফিরে আসে তার মৃতদেহ নিয়ে। মেয়েটির বাবা কাঁধে করে নিয়ে আসে তার মৃতদেহ। ছেলেটির গায়ের কাদা লেগে ওর চুল আর জামা মেটে রং হয়ে গেছে। সারা গায়ে গাছের মরা পাতা। একটা নাকে আর একটা কানে শ্যাওলা ঢুকে সবুজ রং হয়ে গেছে। সবাই ডেডবডি নিয়ে আসছে, সবার মুখ শুকনো করুণ, লজ্জিত যেন, মাথা নিচু।
ছেলেটি দুরন্ত ছিল। এতই দুরন্ত ছিল যে এড়াতে চাইলেও তাকে এড়ানো যেতো না। মেয়েটি তার সাথে খেলত । দোলনায় দুলত। ফায়ার প্লেসের কাঠ উঠোনে জড়ো করে তার উপর থেকে লাফ দিতো। মাটি খুড়ে তার সাথে আলু তুলত, অশ্ব আর অশ্বারেহী খেলত রাখাল সেজে। গাছের ডাল ভেঙে বনবন করে ঘুরাতে ঘুরাতে। মেয়েটা স্টিভকে যতটা পছন্দ করত তার চেয়ে বেশি অপছন্দ করত। তবু সে তার দুরন্তপনায় সায় দিত। স্টিভের বাড়িতে শেষকৃত্য করার জায়গা ছিল না। শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করল মেয়েটির মা তাদের বাড়িতে। মেয়েটি একটা সাদা ড্যাফোডিল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাদা মোজা পরা তার পায়ের গোঁড়ালি চুলকাচ্ছিল । সে বিষয়টিও বাদ যায়নি মুনরোর কুশলী কলম থেকে। শেষকৃত্যে তার বাবা যখন গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরে এলো আর মা বাদামি রঙের ভেলভেট ড্রেস তখন ওদের দেখে ঘৃণা হলো মেয়েটির, সাথে রাগ।
বিশ বছর পর আবার গল্পের যবনিকা উঠল। মেয়েটি তার স্বামী এন্ড্রু আর দুই সন্তান সিনথিয়া আর মেগকে নিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছে অন্টারিও। যাকে ওরা বলত ‘আমাদের বাড়ি।’ পথের নানা বর্ণনা। একটা মরা হরিণ পথে পড়ে থাকাও লেখকের চোখ এড়ায় না। লেটুস পাতার জন্য এন্ড্রুর বিরক্তি পুরুষের আধিপত্যবাদকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। প্রচন্ড গরমে একটা সুইমিং পুলে গোসল করতে যাওয়ার পর ছোট মেয়ে মেগকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যখন মনে হচ্ছিল মেয়েটি আর বেঁেচ নেই তখন মেয়েটি সাঁতার কেটে ফিরে আসে। গার্ড দুজনের প্রেমালাপ এবং নির্রিপ্ততা, তাদের চুমু খাওয়া দেখছিল সিনথিয়া হা করে। মেয়েটির বার বার মনে পড়ছিল স্টিভ গলির সেই মৃতদেহের কথা। জাদ–বাস্তবতায় নিয়ে আবার বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনেন আমাদের লেখক এক ধাক্কায় । আর সবচেয়ে বেশি ধাক্কা লাগে যখন স্বামী এন্ড্রু বলে, তার মা জানিয়েছেন রজারের এই গাড়িটা পছন্দ নয় । রজার এন্ড্রুর খালার স্বামী । এন্ড্রুর বাবা মারা যায় ওদের ছেলেবেলায়। মা একটা ডিপার্টমেন্টাল শপে কাজ করে। ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছে রজারের সহায়তায়। ওরা প্রাইভেট স্কুলে পড়েছে । সব খরচ জুগিয়েছে রজার। সে গাড়িটা পছন্দ করেনি কারণ গাড়িটা ছোট। এন্ড্রুর মা চিঠিতে লিখে জানিয়েছে। এ কথা বলার পর মেয়েটি বলে, ‘গাড়ি ছোট হোক বা বড় উনি নাক গলাবার কে?’ এখানে ওই মা এবং ভদ্রলোকের সম্পর্কের কোন বর্ণনা বা পরিচয় না দিলেও একটি বাক্য অনেক কিছুই বুঝিয়ে দেয়। যা শুধুমাত্র একজন বড় লেখকের পক্ষেই সম্ভব। গল্পের বিস্তারের মাঝে আমরা খুঁজে পাই মেয়েটির বাবার টার্কিস খামার আর স্বামী এন্ড্রুর ওর বাবা আর তার পরিবেশকে অপছন্দের কথা। এখানে মুনরোর শৈশবকে খুঁজে পাই আমরা।
মুনরোর ‘দি আই’ ও ‘মাউন্ট সিটি মন্টানা’ দুটো গল্পই প্রথম পুরুষে লেখা। প্রথম পুরুষে লেখা গল্প কতটা জোরদার হতে পারে মুনরো তা দেখিয়েছেন।
মুনরো সরল গদ্যে মানুষের জটিল মানস হাজির করেন তাঁর ছোটগল্পে। গল্পের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা বলেন মুনরো। তবে শুধু গল্পেই বলেন না, বাস্তব জীবনেও তাঁর সঙ্গে তাঁর নিকটজনদের সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৯৭ সালে এলিস মুনরো বড় মেয়ে শিলা মুনরোকে তাঁর জীবনী লিখতে বলেন। তিনি যা লিখেছেন সেটা জীবনী না হয়ে বরং স্মৃতিকথা হয়েছে বলা যায়। তাঁর মায়ের ‘লাইভস অব গার্লস অ্যান্ড উইমেন’ বইটির নামের সঙ্গে মিল রেখে লেখেন এই স্মৃতিকথা। নাম দেন ‘লাইভস অব মাদারস অ্যান্ড ডটারস : গ্রোইং আপ উইথ এলিস মুনরো’। বইটি প্রকাশ করন ২০০১ সালে। শিলা যাতে বইটি নিরিবিলি লিখতে পারেন সে জন্য তাঁর বাচ্চাদের দেখাশোনা করেন এলিস মুনরো। শিলা লিখেছেন, এলিসের কৈশোরেই তাঁর মা পারকিনসনস রোগে আক্রান্ত হন। রান্না করা, বাচ্চাদের আদব-কায়দা শেখানোসহ মাতৃত্বের সব দায়িত্ব পালন, পরিবারের অন্য কাজকর্ম সবই করেছেন ঠিকমতোই। কাজ করার সময় সমান্তরালে কল্পনার ভেতরে সাজিয়েছেন গল্পের ডালপালা। পরিবারের অন্য সদস্যরা অবশ্যই তাঁর লেখার কাজটিকে সম্মানের চোখে দেখতেন। ঘরের কোণে টাইপরাইটারে তিনি যখন লিখতে বসতেন, তাঁর স্বামী জিম মুনরো বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে ঘুরতে যেতেন, যাতে তিনি নিরিবিলি পরিবেশে লেখা চালিয়ে যেতে পারেন। এভাবে লিখে প্রায় ২০ বছর নিয়মিত বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেন। তারপর ১৯৬৮ সালে প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম গল্প সংকলন ‘ডান্স অব দ্য হ্যাপি শেডস’।
মায়ের খ্যাতির বিস্তার দেখতে দেখতেই বড় হতে থাকেন মেয়ে। মেয়ের সমবয়সীরা ছাড়াও তাঁর শিক্ষক এবং অন্য বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাঁদের সম্পর্কের কথা জানতেন। মা- মেয়ের সম্পর্ক জানার পর মাঝে মাঝে অন্যরা যেসব মন্তব্য করতেন সেগুলো শুনে শিলা খানিকটা বিব্রতও হয়েছেন : অনেকে মায়ের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করার চেষ্টা করেছেন। কারণ মেধা, সৃজনক্ষমতা, জীবনীশক্তি এসবে মা কত এগিয়ে। তবে তাতে মা- মেয়ের বন্ধুত্বের ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়েনি। পরবর্তী জীবনেও দুজন যতটা সম্ভব নিকটে থাকার, যত বেশি সম্ভব দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করেন। তাঁদের সম্পর্কে একটি মজার প্রসঙ্গ হলো, মাঝে মাঝে মেয়েই মায়ের ভূমিকা নিয়েছেন এবং মা হয়েছেন মেয়ের মতো। মা বাইরে গেলে তাঁর জন্য গর্বিত মায়ের মতো অপেক্ষা করেছেন শিলা। যেন পেছনে তিনি সজাগ আছেন, মেয়ের নিরাপদে ফিরে আসার অপেক্ষায় আছেন। বইয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করা, সাক্ষাৎকার দেওয়া, পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এলিস মুনরো এসব কাজে বাইরে গেলে তাঁর জন্য বয়সী মায়ের মতোই অপেক্ষায় থেকেছেন শিলা। তখন তাঁর মনের ভেতরে এক ধরনের আগ্রহ থাকে : মা কখন ফিরবেন, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। কারণ এলিস মুনরো সত্যিই বাইরের অভিজ্ঞতা মেয়ের কাছে বলে আনন্দ পান।
শিলাও তাঁর মাকে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকেন মানবিক স্বভাবের মৌলিক চাহিদাসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে। তাঁর ক্ষুধা আছে, তাঁর যৌনতা আছে, তিনি কখনো কখনো পরাজিত হন, জর্জরিত হন। সন্তানের মধ্যে তখন এক ধরনের আকুতি থাকে। মায়ের জন্য তেমন আকুতিও প্রকাশ পেয়েছে শিলার এ বইটিতে।
মোটকথা, মা- মেয়ে উভয়েই যাঁর যাঁর জায়গা থেকে একজন আরেকজনকে সমর্থন দিয়ে যান।
মুনরো যে জনপদে জন্মেছেন, যে জনপদে বেড়ে উঠেছেন সেটাই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। অন্য কোনো ল্যান্ডস্কেপ, দেশ, লেক বা শহর তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না বলে তাঁর ধারণা । আর তিনি ওখান থেকে কখনো কোথাও যাবেনও না।
তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া
ড. আফরোজা পারভীন
কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, কলামলেখক
অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব
বিষয়: ড. আফরোজা পারভীন

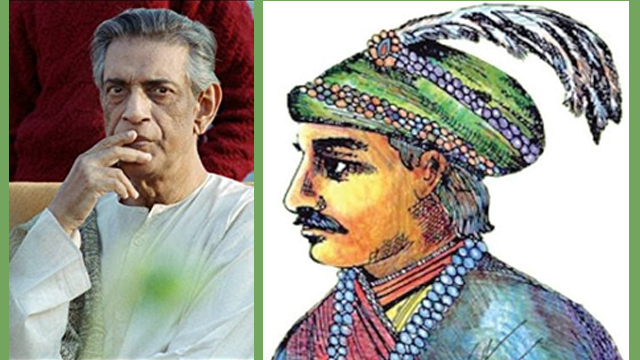
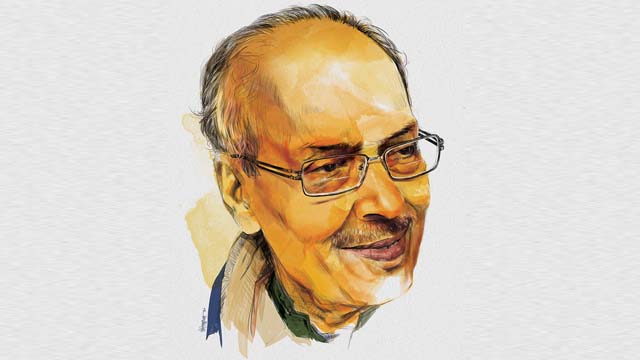



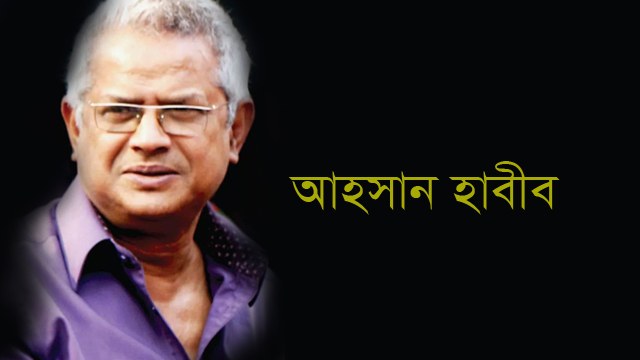


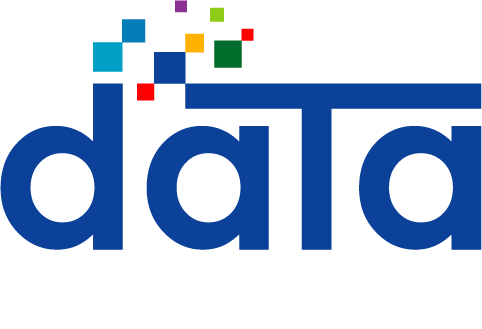
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: