ইলা মিত্র : নাচোলের হার না মানা রাণীমা : আফরোজা পারভীন
প্রকাশিত:
২৫ জুন ২০২০ ০০:০৮
আপডেট:
২৫ জুন ২০২০ ২১:০৫

ইলা মিত্র ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল ইলা সেন। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন বৃটিশ সরকারের অধীন বাংলার একাউন্টেন্ট জেনারেল। তাঁদের আদি নিবাস ছিল তৎকালীন যশোরের ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে। বাবার চাকুরির সুবাদে তাঁরা কলকাতায় বসবাস করতেন।
তিনি কলকাতা শহরে বেড়ে ওঠেন। লেখাপড়া করেন কলকাতার বেথুন স্কুল ও বেথুন কলেজে। এই কলেজ থেকে তিনি ১৯৪৪ সালে স্নাতক শ্রেণিতে বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন।
পড়াশুনার মতো খেলাধুলায়ও তুখোড় ছিলেন ইলা সেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্য জুনিয়র এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন। সাঁতার, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন । তিনিই প্রথম বাঙালি মেয়ে যিনি ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অলিম্পিক বাতিল হয়ে যাওয়ায় তাঁর অংশগ্রহণ করা হয়নি। খেলাধুলা ছাড়াও গান, অভিনয়সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।
বেথুন কলেজে বাংলা সাহিত্যে বি.এ. সম্মানের ছাত্রি থাকাকালীন রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন ইলা সেন । ১৯৩৬-৪২ সালের মধ্যে ইলা মিত্রের নাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৩ সালে ইলা সেন কলকাতা মহিলা সমিতির সদস্য হন। রাওবিল বা হিন্দু কোড বিল এর বিরুদ্ধে সে বছর মহিলা সমিতি আন্দোলন শুরু করে। সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তিনি এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তিনি অনেক প্রচার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নারী আন্দোলনের এই কাজ করতে করতে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন।
১৯৪৫ সালে ইলা মিত্রের বিয়ে হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের জমিদার মহিমচন্দ্রের পুত্র রমেন মিত্রের সাথে। রমেণ মিত্র ছিলেন বিপ্লবী, কমিউনিস্ট নেতা । বিয়ের পর তিনি শ্বশুরবাড়ি রামচন্দ্রপুর হাটে চলে আসেন। রমেণ মিত্র রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের সন্তান। পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী অন্দরমহলেই থাকতেন ইলা মিত্র। দমবন্ধ হয়ে আসতো তাঁর। শুধু প্রার্থনা করতেন এক পসলা নির্মল বাতাসের। রমেণ মিত্রের বন্ধু আলতাফ মিয়া কৃষ্ণগোবিন্দপুর হাটে মেয়েদের একটি স্কুল খোলেন। এলাকার জনগণ রমেণ মিত্রের কাছে দাবি জানান নিরক্ষর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব নিতে হবে বধূমাতা ইলা মিত্রকে। মাত্র তিনজন ছাত্রি নিয়ে স্কুলটি শুরু করেন ইলা মিত্র । তিনমাসের মধ্যে ছাত্রি সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০/৫০-এ ।
স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল দারুণ। গভীর শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক ছিল দু’জনের মধ্যে। দু’জনই মার্কসবাদের রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন মার্কসবাদই একমাত্র নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত মানুষের মুক্তির পথ। মার্কসবাদই সারাবিশ্বের মানুষের মুক্তির পথ । রমেণ মিত্রের একান্ত সহযোগিতায়ই ধীরে ধীরে ইলা মিত্র হয়ে উঠেন ‘রাণী মা’- তেভাগার লড়াকু যোদ্ধা।
স্বামী রমেণ মিত্রের কাছে তিনি জমিদার ও জোতদারের হাতে বাংলার চাষিদের বঞ্চনা, শোষণ এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনের বীরত্বগাথা শোনেন। কমিউনিস্ট রমেণ মিত্র জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে পারিবারিক ঐতিহ্য ও মোহ ত্যাগ করে কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ক্রমাগত শোষণ কৃষকের মনে বিক্ষোভের জন্ম দেয়। ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় ‘সর্ব ভারতীয় কৃষক সমিতি’। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার উদ্যোগে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব দেয় ‘ফাউন্ড কমিশন’। এই কমিশনের সুপারিশ ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে চাষিদের সরাসরি সরকারের প্রজা করা এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুইভাগের মালিকানা প্রদান করা। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। চল্লিশের দশকে এসব আন্দোলনে ইলা মিত্র নেতৃত্ব দেন।
১৯৪২-৪৩ সালে সমগ্র বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । এ সময় কৃষকের ওপর শোষণের মাত্রা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তিনভাগের দুইভাগ ফসল, কৃষকের এই দাবি নিয়ে বেগবান হতে থাকে তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৬-৪৭ সালে দিনাজপুরে কমরেড হাজী দানেশের প্রচেষ্টায় সংগঠিত হয় যুগান্তকারী তেভাগা আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি চাষিদের সংগঠিত করে আন্দোলনকে জোরদার করতে থাকে। পার্টি থেকে রমেণ মিত্র ও ইলা মিত্রকে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে তেভাগা আন্দোলনকে জোরদার করতে বলা হয়। ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় সেবা ও পুনর্বাসনের কাজ করতে এগিয়ে আসেন। এসময় ইলা মিত্র নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রাম হাসনাবাদে পুনর্বাসনের কাজে চলে যান।
মোগল আমল পর্যন্ত জমির মালিক ছিল কৃষক। তারা এক তৃতীয়াংশ বা কখনো কখনো তার চেয়েও কম ফসল খাজনা হিসেবে জমিদার বা স্থানীয় শাসনকর্তার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে প্রদান করতেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সব ওলোট পালট করে দিলো। জমিদার ও কৃষকদের জীবনে এলো অনেক পরিবর্তন। জমির মালিক হলো জমিদার। সে সরাসরি কর দেবে বৃটিশ রাজকে। জমিদাররা জমির পরিমাণ ও উর্বরতা অনুযায়ী ব্রিটিশদের খাজনা দিত। জমিদারদের সঙ্গে ফসল উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ সময় জমিদার ও কৃষকদের মাঝখানে জোতদার নামে মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। জমির সাথে জমিদারদের কোনো সম্পর্ক না থাকায় এই মধ্যস্থতাকারীদের কাছে জমি ইজারা দিতেন জমিদাররা। কৃষকদের থেকে দূরে থাকতেন জমিদার। জোতদারি ও জমিদারি প্রথা ক্ষুদ্র কৃষকদের শোষণের সুযোগ করে দেয়। খাজনা আদায়ের জন্য জোতদাররা এদের দাসের মতো ব্যবহার করেন। সেই অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় ‘সর্বভারতীয় কৃষক সমিতি’।
ইজারাদার যেকোনো উপায়ে অর্থ আদায় ও নিজের লাভ খুঁজতো। ১৯৪৬-৪৭ সালে আধিয়ারী ব্যবস্থায় অর্ধেক ফসল দাবি করে বসে নতুন জমির মালিকেরা। সূর্যাস্ত আইনের ফলে অনেক প্রাচীন জমিদারী শেষ হয়ে যায়। তাদের বদলে জমিদারী কিনে নেয় নব্য ব্যবসায়ীরা। শহরায়ন আর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে অনেক জমিদার শহরমুখী হচ্ছিলেন। কৃষকদের সাথে জমিদারদের সৃষ্টি হওয়া এই দূরত্বকে কাজে লাগায় ইজারাদারেরা। কৃষকদের উপর চলতে থাকে অত্যাচার। মোটামুটি স্বচ্ছল কৃষকেরা হয়ে যান বর্গাচাষী। দরিদ্র এই কৃষকরা মুখ বুজে সহ্য করে নেয়নি এসব অবিচার। তারা রুখে দাঁড়িয়এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাছাড়া জনসাধারণের কাছ থেকে হাটের ' তোলা' ও ' লেখাই'সহ নানা কর আদায় করা হতো। এসব বন্ধের জন্য আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৪৬ সালে কিছু বর্গাচাষী ধান কেটে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। আধিয়ারির নিয়ম অনুযায়ী কৃষকের রক্ত জল করা ফসল কাটার পর যাবে জমির মালিক অথবা জোতদারের বাড়িতে। সেখানে ফসল ও খড়ের সমান ভাগাভাগি হবে। কিন্তু যেহেতু জমির ফসলে বীজ থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যয় ও প্রতিদিনের পরিশ্রম কৃষকের, তাই অর্ধেক ফসলের অধিকার দাবি করা কৃষককে পথে বসানোর সামিল ছিল। তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকদের ভেতর আন্দোলনটি সংগঠিত করে তোলে কম্যুনিস্ট পার্টি। এ সময় ইলা মিত্রের স্বামী রামেন্দ্র মিত্রকে তেভাগার আদর্শ ছড়িয়ে দিতে মনোনীত করে পার্টি। তখন ইলা মিত্র স্বামীর সাথে পায়ে হেঁটে কাদা-বন-জঙ্গল পেরিয়ে কৃষকদের একত্র করতে কাজ করেছেন। যশোর, দিনাজপুর, রংপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, চব্বিশ পরগণা, খুলনাসহ মোট ১৯টি জেলায় আন্দোলন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লেও তীব্র হয়ে ওঠেনি পূর্ববাংলায়। অনেক ভূমিমালিক স্বেচ্ছায় কৃষকদের তেভাগা অধিকার দিতে রাজি হন। ১৯৪৮-৫০ সালে দ্বিতীয় দফায় তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। পাকিস্তান সরকার আর পাঁচটা আন্দোলনের মতোই তেভাগা আন্দোলনকেও ভারতের ষড়যন্ত্র বলে খেতাব দেয়। ইলা মিত্র ছিলেন এই সময়ের প্রধান পথ প্রদর্শকদের একজন।
ইলা মিত্রকে নিয়ে কবি গান বেধেছিলেন:
ইলা মিত্র নারী
আইন করিল জারী
আধি জমি ত্রিফুটি ভাগ
জিন হলো সাত আড়ি ভাই
জিন হলো সাত আড়ি ।
গরিব কৃষকরা যাতে তাদের ন্যায় অধিকার আদায় করতে পারে, আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে সেটাই ছিল ইলার সংগ্রাম।
১৯৪৭-এ দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হয়। ইলা মিত্র ও তার স্বামীকে আত্মগোপনে থাকতে হয় এসময়।
১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ইলা মিত্র ও রমেন মিত্র। ছত্রভঙ্গ কৃষকদের সংগঠিত করতে ইলা মিত্র ছুটে যান গ্রাম থেকে গ্রামে। ১৫০ জন কৃষককে পুলিশ হত্যা করে। নাচোল কৃষক আন্দোলন চিরতরে বন্ধ করে দিতে শাসকগোষ্ঠী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।
১৯৪৮ সাল। ইলা মিত্র অন্তঃসত্তা। সন্তান প্রসবের জন্য তিনি গোপনে কলকাতায় যান। পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এক মাস বয়সের ছেলেকে শাশুড়ির কাছে (রামচন্দ্রপুর হাটে) রেখে তিনি আবার ফিরে আসেন নাচোলে। ১৯৪৯ সালে তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক সংগঠিত হয়। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে জোতদার, মহাজনদের দল। ওই বছর কৃষকের ধান জোতদারদের না দিয়ে সরাসরি কৃষক সমিতির উঠোনে তোলা হয়। ফলে সংঘর্ষ বাধে। নাচোলে সাঁওতাল ও ভূমিহীনদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী তীরন্দাজ ও লাঠিয়াল বাহিনী। এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন মাতলা মাঝি। এভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ইলা মিত্র ও রমেণ মিত্র। নাচোল অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের বাস্তব রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা।
১৯৫০ সালে জোতদার ও ভূমি মালিকেরা নাচোলের ভিতর এবং আশেপাশে তেভাগা কার্যকর করতে বাধ্য হয়। সরকারের পুলিশ বাহিনী গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। তেভাগার বিদ্রোহীরা এ গ্রামে লুকিয়ে আছে এমন খবর পেয়ে ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি পুলিশ বাহিনী চন্ডীপুর গ্রামে আসে। গ্রামবাসী সংগঠিত হয়ে পুলিশ বাহিনীকে পাল্টা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে উত্তেজিত গ্রামবাসী ওই পুলিশ কর্মকর্তা ও পাঁচ জন পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করে। এই ঘটনার দু’দিন পর ৭ জানুয়ারি শুরু হলো পুলিশের প্রতিশোধ। দুই হাজার সেনা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযান শুরু করে। বারোটি গ্রাম ঘেরাও করে তছনছ করে। ঘরবাড়ি ধ্বংস করে। গুলি চালিয়ে হত্যা করে অসংখ্য গ্রামবাসীকে। নারীদের ধর্ষণ করে। শিশুদের উপর চালায় যৌন নির্যাতন। আন্দোলনকারী নেতা-কর্মীরা যে যার মতো আত্মগোপনে চলে যায়। ইলা মিত্র ৭ জানুয়ারি সাঁওতাল বেশ ধারণ করে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ভারত সীমানা পার হওয়ার সময় তিনিসহ আরো অনেক নেতা-কর্মী রোহনপুর রেলওয়ে স্টেশনে ধরা পড়ে যান। তাদের ধরে আনা হয় নাচোল স্টেশনে। পুলিশ তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এই অত্যাচারে ইলা মিত্রের সাথীদের মধ্যে আনুমানিক ৮০/৯০ জন মারা যায়।
কমরেড ইলা মিত্রের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হল। পুলিশ অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে তার স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে। টানা চার দিন অত্যাচারের পর নাচোল স্টেশন থেকে ইলা মিত্রকে নবাবগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে আনা হয়। সে সময় তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। গায়ে ছিল প্রচন্ড জ্বর। কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে নানা ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়। ইলা মিত্রের একটি স্মৃতিচারণ তুলে ধরা হলো:
ওরা প্রথম থেকেই নির্দয় ভাবে মারতে শুরু করলো। শুধু আমাকে নয়, আমাদের সবাইকেই। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে এল নাচোলে। আমি মারপিটের ফলে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, আমার সর্বাঙ্গে বেদনা। ওরা আমাকে একটা ঘরের বারান্দায় বসিয়ে রাখল। আমাদের সঙ্গে যে সকল সাঁওতাল কর্মীরা ছিল, আমার চোখের সামনে তাদের সবাইকে জড় করে তাদের উপর বর্বরের মত মারপিট করে চললো। আমি যাতে নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখতে পাই, সেজন্যই আমাকে তাদের সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।
ওরা তাদের মারতে মারতে একটা কথাই বারবার বলছিল, আমরা তোদের মুখ থেকে এই একটা কথাই শুনতে চাই, বল, ইলা মিত্র নিজেই পুলিশদের হত্যা করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। এই কথাটুকু বললেই তোদের ছেড়ে দেব। কিন্তু যতক্ষণ না বলবি, এই মার চলতেই থাকবে। মারতে মারতে মেরে ফেলব, তার আগে আমরা থামব না।
কথাটা তারা যে শুধু ভয় দেখাবার জন্য বলছিল, তা নয়, তারা মুখে যা বলছিল, কাজেও তাই করছিল। ও সে কি দৃশ্য! আর সেই দৃশ্য আমাকে চোখ মেলে দেখতে হচ্ছিল। এ কি শাস্তি! কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই হিংস্র পশুর দল আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। রক্তে ওদের গা ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু কারু মুখে কোন শব্দ নাই, একটু কাতরোক্তি পর্যন্ত না। ওরা নিঃশব্দ হয়ে ছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে কেঁদে ফেললাম আমি। এই দৃশ্য আমি আর সইতে পারছিলাম না। মনে মনে কামনা করেছিলাম, আমি যেন অজ্ঞান হয়ে যাই। কিন্তু তা হল না, আমাকে সজ্ঞান অবস্থাতেই সব কিছু দেখতে হচ্ছিল, কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, এত দুঃখের মধ্যেও আমাদের এই বীর কমরেডদের জন্য গর্বে ও গৌরবে আমার বুক ভরে উঠেছিল। একজন নয়, দু’জন নয়, প্রতিটি মানুষ মুখ বুজে নিঃশব্দ হয়ে আছে, এত মার মেরেও ওরা তাদের মুখ খোলাতে পারছে না। এমন কি করে হয়! এমন যে হতে পারতো এ তো আমি কল্পনাও করতে পারিনি।
মনে মনে একটা কথা আবৃত্তি করে চলেছিলাম, হে বীর সাথীরা আমার, তোমাদের কাছ থেকে যে শিক্ষা আমি আজ নিলাম, তা যেন আমার বেলায় কাজে লাগাতে পারি। আমার উপর অত্যাচার এই তো সবে শুরু হয়েছে। আমি জানি, এরপর বহু অত্যাচার আর লাঞ্ছনা আমার উপর নেমে আসবে। সেই অগ্নি-পরীক্ষার সময়, হে আমার বীর সাথীরা, আমি যেন তোমাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিঃশব্দে মুখ বুজে থাকতে পারি। আর যদি মরতেই হয়, যেন অমনি নিঃশব্দে মরে যেতে পারি।
প্রচন্ড তর্জন গর্জনের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম, চেয়ে দেখি, হরেককে দলের মধ্য থেকে মারতে মারতে বার করে নিয়ে আসছে। ওদের মুখে সেই একই প্রশ্ন, বল, ইলা মিত্র সে-ই পুলিশদের হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিল। না বললে মেরে ফেলব, একদম মেরে ফেলব। আমি চেয়ে আছি হরেকের মুখের দিকে। অদ্ভুত ভাববিকারহীন একখানি মুখ। অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্যপানে তাকিয়ে আছে। ওদের এত সব কথা যেন তার কানেই যাচ্ছে না। ক্ষেপে উঠল ওরা। কয়েক জন মিলে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। তারপর ওরা ওদের মিলিটারি বুট দিয়ে তার পেটে বুকে সজোরে লাথি মেরে চলল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, হরেকের মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তারপর তার উপর ওরা আরও কতক্ষণ দাপাদাপি করল। একটু বাদেই এক খন্ড কাঠের মত স্থির হয়ে পড়ে রইল হরেক। ওদের মধ্যে একজন তাকে নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, ছেড়ে দাও, ওর হয়ে গেছে। এই বলে ওরা আর এক জনকে নিয়ে পড়ল।
মরে গেছে। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে হরেক। অনেক দিন আগেকার পুরানো একটা কথা মনে পড়ে গেল। একদিন হরেককে পার্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজের সময় তার দেখা মেলেনি। এজন্য কৈফিয়ত চাইলে পরে সে বলেছিল, তার গরুটা হারিয়ে যাওয়ায় সে তাকে খোঁজ করতে বেরিয়েছিল। সেই জন্যই সে সময় মত উপস্থিত থাকতে পারেনি। এজন্য অনেকের সামনে তাকে তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। তারপর থেকে তার উপর কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হতো না। এটা বুঝতে পেরেছিল হরেক। এই নিয়ে সে এক দিন অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিল, আমাকে কি মনে করেন আপনারা? জানেন, প্রয়োজন হলে পার্টির জন্য আমি জীবন দিতে পারি? এই ধরনের বাগাড়ম্বর অনেকেই করে। তার এই কথায় কেউ ততটা আমল দেয়নি। কিন্তু আজ? আজ হরেক তার জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেল, সেদিন সে যা বলেছিল, তা বাগাড়ম্বর নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য।
আমাদের ছেড়ে চলে গেছে হরেক। আর কোন দিন ফিরে আসবে না। একটু আগেই আমি কেঁদেছিলাম। কিন্তু এখন আমার সমস্ত কান্না শুকিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে ভিতর থেকে প্রচন্ড একটা জিদ মাথা তুলে জেগে উঠছে। আমার মন বলে চলেছে, মারুক, মারুক, ওরা আমাকেও এমনি করে মারুক। আর মনে হচ্ছে, এই যে আমাদের কয়েক শ’ সাথী, এদের মধ্যে কাউকে দিয়ে ওরা কথা বলাতে পারবে না। কিছুতেই না। ওদের হার হয়েছে। ওদের হার মানতে হবে।
- ইলা মিত্র
(সত্যেন সেনের বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন বইয়ের পৃষ্ঠা: ১০৬-১০৯ থেকে সংগৃহীত।)
একে নারী, তার ওপর কমিউনিস্ট, অস্ত্র হাতে তেভাগা আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন এ কারণে পুলিশের আক্রোশ তাঁর উপর বেশি ছিল। বাঁশকল, শরীরের নাজুক অংশে বুটের আঘাত, বিবস্ত্র করে প্রহার, অনাহারে রাখা, ধর্ষণ, আপত্তিজনক মন্তব্য এমন নানা ধরণের অত্যাচার চালানো হয়েছিল ইলা মিত্রর ওপর।
এরপর শুরু হয় আইনের খেলা। ইলা মিত্র, রমেন্দ্র মিত্র ও মাতলা মাঝি (ইলা মিত্রকে গোপনে সাঁওতালদের প্রশিক্ষণ দিতে সহায়তাকারী) কে প্রধান আসামী এবং শতাধিক সাঁওতাল কৃষকের বিরুদ্ধে পুলিশ হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি রাজশাহী কোর্টে উঠে। এটাই কুখ্যাত ‘নাচোল হত্যা’ মামলা।
রাজশাহী আদালতে ইলা মিত্র ইংরেজিতে লিখিত যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর ওপর যে অত্যাচার হয়েছে সে বিষয়ে জানা যায়। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে বলেন, ‘বিগত ০৭.০১.৫০ তারিখে আমি রোহনপুর থেকে গ্রেপ্তার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল থানা হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়। কিন্তু পথে পাহারাদার পুলিশরা আমার ওপর অত্যাচার করে। নাচোলে ওরা আমাকে একটা সেলের মধ্যে রাখে। সেখানে একজন পুলিশের দারোগা আমাকে এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, আমি যদি হত্যাকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি না করি, তাহলে ওরা আমাকে উলঙ্গ করবে।
আমার যেহেতু বলার মত কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার পরনের সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সেলের মধ্যে আটকে রাখে। আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি। এমন কি এক বিন্দু জলও না। ঐ সন্ধ্যায় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এসআইএর উপস্থিতিতে সিপাইরা এসে বন্দুকের বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর ওরা আমার পরনের কাপড় চোপড় ফেরত দেয়। রাত প্রায় বারোটার সময় আমাকে বের করে সম্ভবত এসআইএর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি খুব বেশি নিশ্চিত ছিলাম না। আমাকে যে কামরায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে আমার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ওরা নৃশংস ধরনের পন্থা অবলম্বন করে। আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে ওরা আমার পা দুটোকে লাঠির মধ্যে রেখে ক্রমাগতভাবে চাপ দিতে শুরু করে। ওদের ভাষায় আমার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী ইনজেকশন পন্থায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল।
এ ধরনের অত্যাচার চলার সময় ওরা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল এবং আমার চুল ধরেও টান দিচ্ছিল। কিন্তু আমাকে দিয়ে জোরপূর্বক কিছুই বলাতে সক্ষম হয়নি। এতসব অত্যাচারের দরুণ আমার পক্ষে আর হেঁটে যওয়া সম্ভব ছিল না। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে নিয়ে গেল। এবার পুলিশের সেই দারোগা সিপাহীদের ৪টা গরম ডিম আনার নির্দেশ দিয়ে বলল যে, এবার মেয়েটাকে কথা বলতেই হবে। তারপর শুরু হল নতুন ধরনের অত্যাচার।
৪/৫ জন সিপাহী মিলে জোর করে আমাকে চিত্ হয়ে শুতে বাধ্য করল এবং ওদের একজন আমার গোপন অঙ্গ দিয়ে একটা ডিম ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। সে এক ভয়াবহ জ্বালা। প্রতিটি মুহূর্ত অনুভব করলাম, আমার ভিতরটা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ১৯৫০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সকালে আমার জ্ঞান ফিরে এলো। একটু পরে জনাকয়েক পুলিশ সঙ্গে করে আবার সেই দারোগার আগমন ঘটে। সেলে ঢুকেই সে আমার তলপেটে বুট দিয়ে প্রচন্ড জোরে লাথি মারে। আমি দারুণ ব্যথায় কুঁকড়ে গেলাম। এরপর ওরা জোর করে আমার ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটা লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দিল।
আমি তখন অর্ধ- চৈতন্য অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছি। কোন রকম স্বীকারোক্তি না পেয়ে দারোগা তখন রাগে অগ্নিশর্মা। যাওয়ার আগে বলে গেল, আমরা আবার রাতে আসব। তখন তুমি স্বীকারোক্তি না দিলে, একের পর এক সিপাহী তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাতে দারোগা আর সিপাহীরা আবার এলো এবং আবারো হুমকি দিল স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য। কিন্তু আমি তখনও কিছু বলতে অস্বীকার করলাম। এবার দু জন মিলে আমাকে মেঝেতে ফেলে ধরে রাখল এবং একজন সেপাহী আমাকে রীতিমত ধর্ষণ করতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম’ (তথ্যসূত্র: ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, মুক্তিমঞ্চে নারী, প্রিপ ট্রাস্ট, ১৯৯৯, ঢাকা)।
নাচোল হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডের রায় প্রদান করে ইলা মিত্রকে রাজশাহী জেলে প্রেরণ করা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করা হলে শাস্তির মেয়াদ ১০ বছর কমিয়ে দেয়া হয়।
পুলিশের নির্যাতনে তখন ইলা মিত্রের শারীরিক অবস্থা শঙ্কটাপন্ন। ১৯৫৩ সালে তাঁকে ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৫৪ সালে কমরেড ইলা মিত্রের চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আনা হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসলে মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হকের নির্দেশে ইলা মিত্রের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য গঠিত একটি মেডিকেল টিমের সুপারিশে বলা হয়, ইলা মিত্র নানা ধরনের দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। এসবের চিকিৎসা পূর্ব-বাংলায় সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী এই সুপারিশের ভিত্তিতে নির্দেশ দেন, নাচোল হত্যা মামলার অন্যতম সাজাপ্রাপ্ত আসামী ইলা মিত্রকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেয়া হলো।
ইলা মিত্রকে ভারতে প্রেরণের জন্য অর্থ এবং পাসপোর্ট সংগ্রহে পূর্ব-বাংলার বামপন্থী নেতারা এগিয়ে এসেছিলেন। পাসপোর্ট তৈরিতে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সাহায্য করেন এমনকি ভারত যাওয়ার প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ইলা মিত্রর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎও করেন।
কলকাতা মেডিকেল কলেজে দীর্ঘ আটমাস চিকিৎসাধীন ছিলেন ইলা মিত্র। তিনি একমাত্র পুত্র রণেন মিত্র মোহনের মুখ দেখেন দীর্ঘ ছয় বছর পর। শোষিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কৃষকের মা ইলা মিত্রের মাতৃত্বকে ত্যাগের এই দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।
সুস্থ হয়ে ইলা মিত্র কলকাতা সিটি কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন।
শিক্ষকতার পাশাপাশি ইলা মিত্র পশ্চিম বঙ্গের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির জেলা ও প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ছিলেন।
কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে বিভিন্ন নারী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে তাকে আবারো কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ভীক। তাঁকে থামানো যাবে না। তিনি চারবার বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন।
ইলা মিত্র বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধির নাম। এক মানবতাবাদী নারীর নাম। জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছেন মানুষের জন্য। ভোগ করেছেন অমানুষিক নির্যাতন। তবুও থামেনি তাঁর আদর্শের লড়াই। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সাধারণ মানুষের পাশে ছিলেন। কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়ে শোষিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন আবার শিক্ষকতা করে অগণিত শিক্ষার্থীকে আলোর পথ দেখিয়েছেন।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন তিনি। ভারত সরকার ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী’ হিসেবে ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার অ্যাথলেটিকসে অবদানের জন্য তাকে সম্মাননা দেয়।‘হিরোশিমার মেয়ে’ বইয়ের অনুবাদের জন্য তিনি সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পান।
ইলা মিত্র কলকাতায় স্বামী রমেন্দ্র মিত্র, একমাত্র পুত্র রণেন মিত্র, পুত্রবধু ও নাতি ঋতেনকে নিয়ে জীবনের শেষ সময় কাটিয়েছেন। উপমহাদেশের নারী জাগরণ ও কৃষক আন্দোলনের এই কিংবদন্তি নেত্রী ৭৭ বছর বয়সে ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। আমৃত্যু নিজেকে বাংলাদেশীই ভেবে এসেছেন তিনি। জমিদার বধূ হয়েও সাদামাটা জীবন কাটিয়েছেন। শত শত বিঘা জমি দান করে গেছেন কৃষকদের নামে। বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কৃষক আন্দোলনের নাম যতবার উচ্চারিত হবে ততবার তেভাগার রাণীমা ইলা মিত্রের কথা উঠে আসবে। উঠে আসবে নাচোলের হার না মানা রাণী ইলা মিত্রের নাম। জয়তু ইলা মিত্র।
আফরোজা পারভীন
কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, কলামলেখক
বিষয়: আফরোজা পারভীন

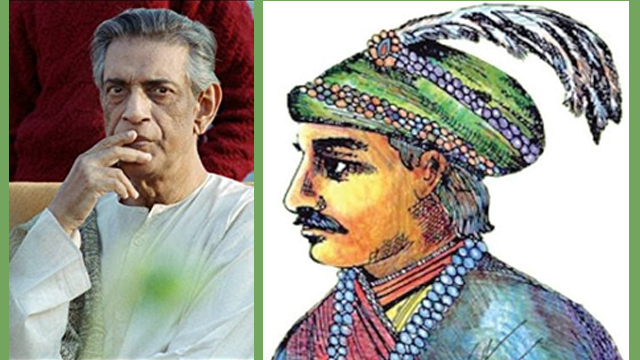
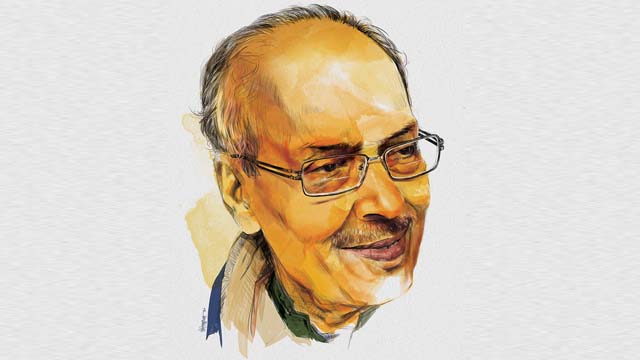



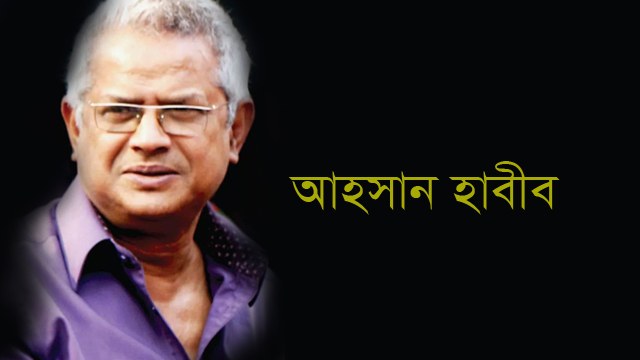


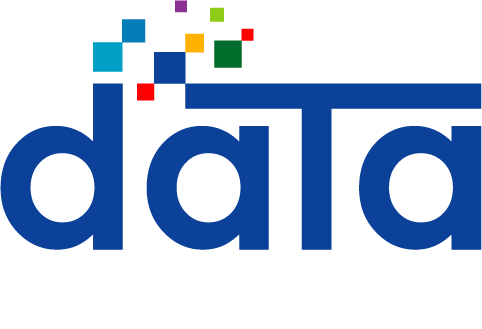
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: